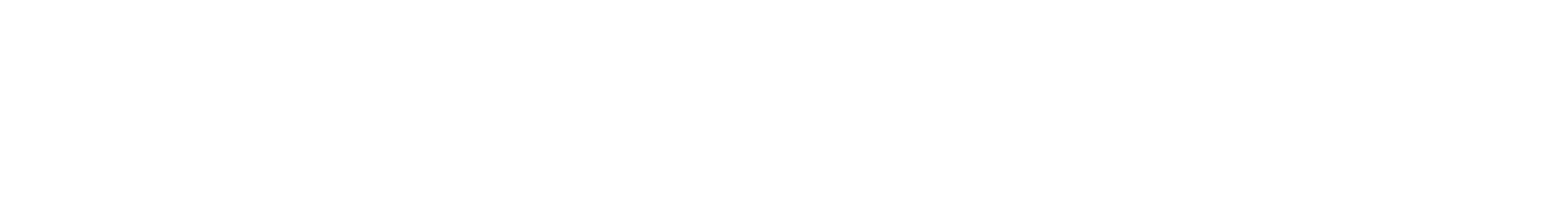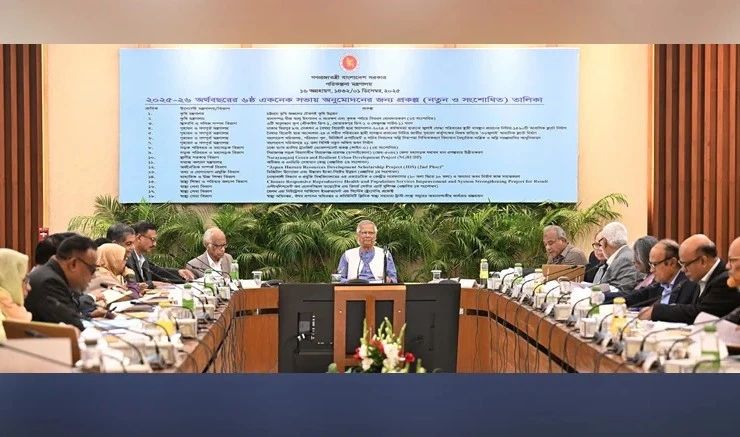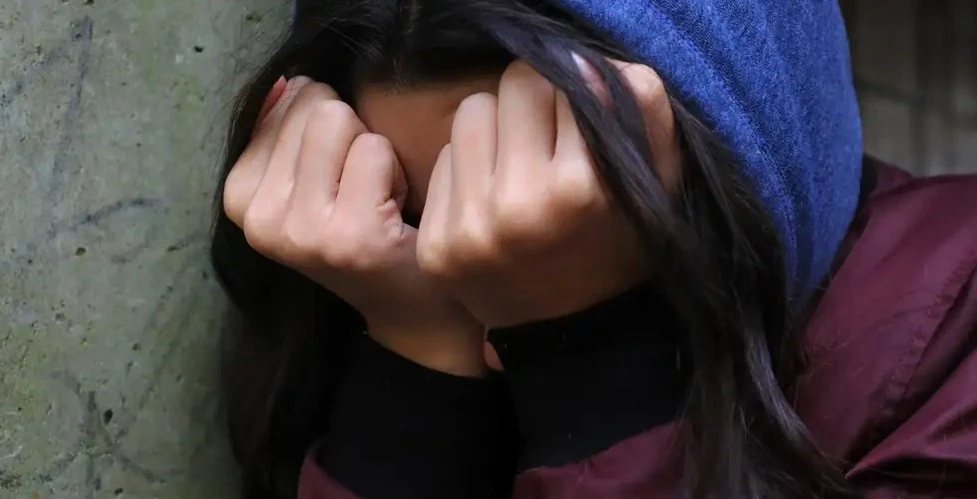সমঝোতা, মধ্যস্থতা ও ন্যায়বিচার: বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার নতুন অধ্যায়
সমঝোতা, মধ্যস্থতা ও ন্যায়বিচার: বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার নতুন অধ্যায়
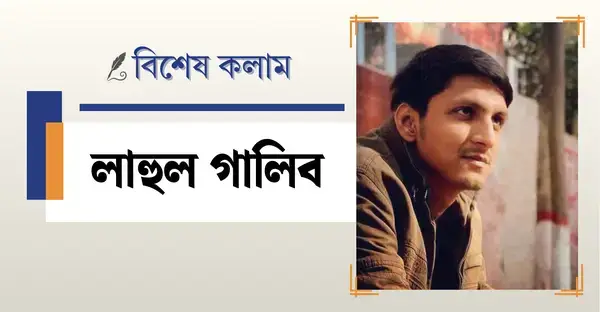
- Author, লাহুল গালিব
- Role, জাগরণ নিউজ বাংলা
সম্প্রতি প্রণীত আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার বিদ্যমান ন্যারেটিভে একটি প্যারাডাইম শিফট এনে দিয়েছে। এখন থেকে যেকোন পারিবারিক বিরোধ নিরসনে আদালতকেই একমাত্র সমাধানের জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হবে না; বরং মামলাপূর্ব বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা/মিডিয়েশনকে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার সিলেটের গ্র্যান্ড সিলেট হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে এটি এখন কার্যকর আইনগত প্রক্রিয়া - যা বিচারব্যবস্থায় অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশনের (এডিআর) কনসেপ্টকে এডোপ্ট করছে। এটি সত্যিকার অর্থেই লিগ্যাল ইন্টারপ্রিটিশনে একটি বিরাট রূপান্তর হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুলের স্টেটমেন্ট সেদিকেই ইন্ডিকেট করে।
প্রথমত, অধ্যাদেশটিতে যেসব বিষয়ে মধ্যস্থতাকে বাধ্যতামূলক করেছে সেটা প্রকৃতপক্ষে একটি বড় আইনি পুনর্বিন্যাস। পারিবারিক বিরোধ, বাবা-মায়ের ভরণপোষণ, বাড়িভাড়া, সম্পত্তি ক্রয় বা বণ্টন, এবং যৌতুক-সংক্রান্ত বিরোধ আদালতে যাওয়ার আগে অবশ্যই মধ্যস্থতার আওতায় আসবে। অর্থাৎ, এ ধরনের দ্বন্দ্বে আর সরাসরি মামলা করা যাবে না। সমঝোতা না হলে পরে মামলা করার সুযোগ থাকবে। এই বিধান বিচারব্যবস্থাকে বিষয়ভিত্তিকভাবে পুনর্গঠন করেছে-যাতে ক্ষুদ্র সামাজিক দ্বন্দ্ব আদালতের দীর্ঘসূত্রতায় আটকে না গিয়ে দ্রুত সমাধানের দিকে এগোয়। এটা স্যোসাইটির স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এবং রিলেশনাল ডায়নামিক্সের কনফ্লিক্টগুলোকে এড্রেস করার জন্যে একটি দারুণ এপ্রোচ।
দ্বিতীয়ত, বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে সরকার প্রথম ধাপে ১২টি জেলায় (সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাঙামাটি) কার্যক্রম শুরু করেছে। এই পাইলট ভিত্তিক রোল-আউট নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারাদেশেই এই প্রসেসের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হবে। তবে স্থানীয় প্রশাসনিক সক্ষমতা ও আদালতের কাঠামোগত জনবল যদি কনফিক্ট রেজুলুশনের ব্যাসিক কনসেপ্টগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকে, তবে প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।
তৃতীয়ত, এর সঙ্গে নতুন ইন্সটিটিউশনাল অরগানোগ্রামও গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে চিফ লিগ্যাল এইড অফিসার পদ যুক্ত করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত মধ্যস্থক/মিডিয়েটর (যেমন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলোঃ মধ্যস্থতাকে দক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করা। তবে এখানেই বড় চ্যালেঞ্জ! যদি প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষতা ও মনিটরিং দুর্বল হয়, তবে এই কাঠামো দ্রুতই পারফরম্যান্স-ফেইলিং পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে। এক্ষেত্রে এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করতে এবং প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘমেয়াদে ইফেক্টিভ ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে আসতে এই স্টাকচারে শান্তি ও সংঘর্ষের থিওরিটিক্যাল অধ্যয়নে পারদর্শী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
চতুর্থত, পলিসি ওয়াইজ এই কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে কিছু বিষয় আমলে রাখা বাঞ্চনীয়। বিশেষত, প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠী ও পারিবারিক নির্যাতনের ভুক্তভোগীরা বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার কারণে ন্যায়বিচারের পূর্ণ সুযোগ নাও পেতে পারেন। ক্ষমতার অসমতা থাকলে জোরপূর্বক সমঝোতার প্রবণতা বাড়তে পারে, যা প্রকৃত ন্যায়বিচারকে সংকুচিত করবে। তাই সুরক্ষা প্রটোকল থাকা অপরিহার্য! যেমন: আইনি পরামর্শ ও কাউন্সেলিংয়ের অবাধ অ্যাক্সেস, সমঝোতার লিখিত ও নির্বাহযোগ্য কাঠামো, এবং আপিল/পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং মিডিয়েশনের সিধান্ত বাস্তবায়নে লিগ্যাল র্যাটিফিকেশন। এগুলো ছাড়া এই উদ্যোগ জনগণের আস্থা বিল্ডআপ করতে সময় নিতে পারে।
পঞ্চমত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, ভারতের লোক আদালত/গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সোসাইটির ইন্টারন্যাল ডিসপিউট রেজুলেশন ম্যাকানিজম, নরওয়ের কনসিলিয়েশন বোর্ড, যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিটি মেডিয়েশন সেন্টার, কিংবা রুয়ান্ডার গাচাচা সব ক্ষেত্রেই আদালতের বাইরে সংলাপ-ভিত্তিক সমাধান দ্রুততা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। তবে সেখানকার সীমাবদ্ধতাও আমাদের জন্য সতর্কবার্তা! মধ্যস্থতা কার্যকর হবে তখনই যখন এটি সম্পর্ক রক্ষা, মর্যাদা পুনর্গঠন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারবে। এখানেই “কনফ্লিক্ট ট্রান্সফরমেশন” ও “রিস্টোরেটিভ জাস্টিস”এর ধারণাগুলো প্রাসঙ্গিক। মধ্যস্থতা যদি পক্ষগুলোর মধ্যে সম্পর্ককে টেকসই করে, তবে এটি কেবল মামলা কমানোর কৌশল নয়, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতার উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।
পরিশেষে, এই উদ্যোগের ভবিষ্যৎ লিগ্যাল ইমপ্লিকেশন কার্যত স্পষ্ট: এই উদ্যোগ যদি পাইলট প্রকল্প-ভিত্তিক মূল্যায়ন, প্রশিক্ষিত নিরপেক্ষ মিডিয়েটর, আইনি সহায়তার অবাধ এক্সেস, স্ট্রং মনিটরিং এবং আপিল-সুবিধার সঙ্গে সমন্বিত হয়, তবে এটি বিচারব্যবস্থায় নিসঃন্দেহে একটি টেকসই সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যথায়, যদি কেবল মামলার সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচারকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং, আইনটির প্রকৃত সফলতা নির্ভর করবে এটি কীভাবে ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক শান্তি ও সম্পর্ক রক্ষার প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়।
(লেখক একজন আইনি শিক্ষানবিশ ও সংঘাত বিশ্লেষক, যিনি সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গবেষণায় নিয়োজিত।)
আপনার প্রতিক্রিয়া জানান
মন্তব্যসমূহ
এই সংবাদের জন্য এখনো কোনো মন্তব্য নেই।