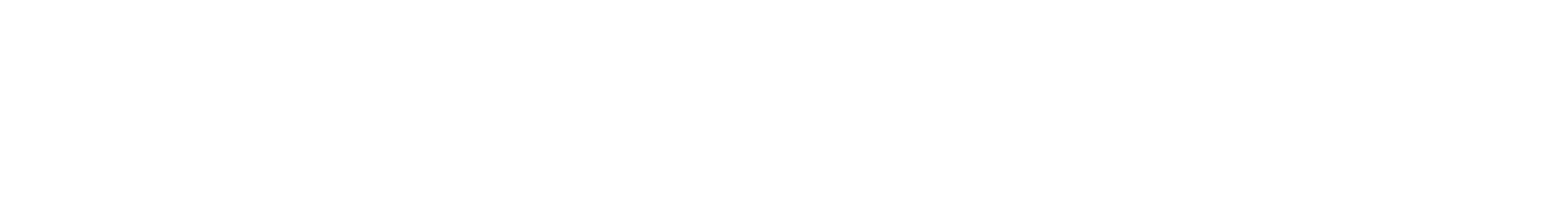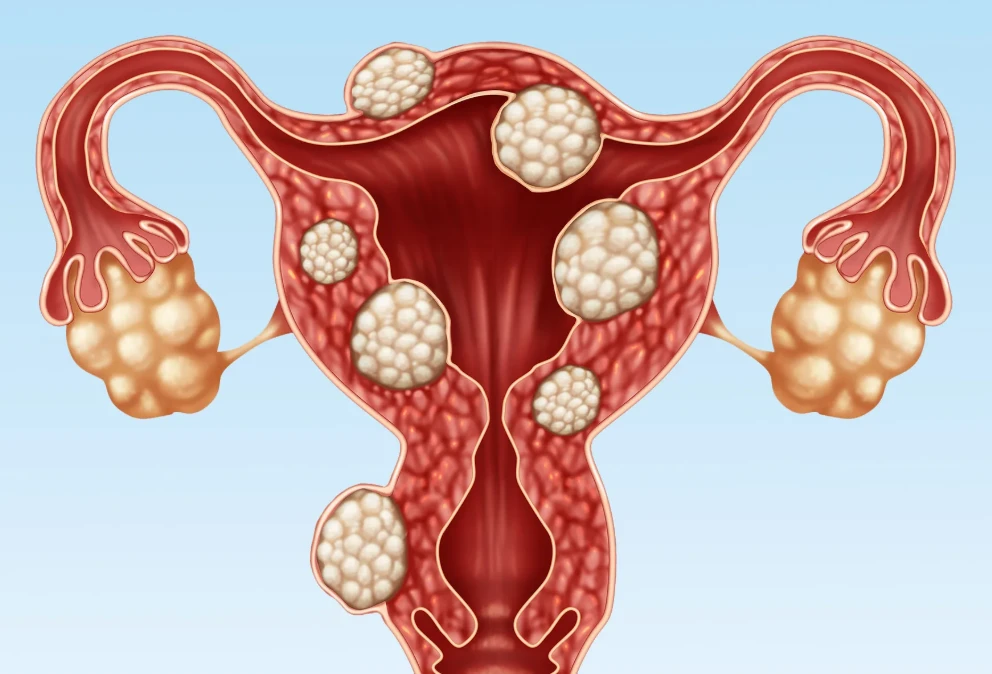বিপদে নীরব ভিড়,এটাই কি নতুন স্বাভাবিকতা? জানুন 'বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট'-এর ভয়ংকর মানসিক রহস্য

- Author,
- Role, জাগরণ নিউজ বাংলা
মানুষ হিসেবে আমরা সহানুভূতিশীল, অন্তত সেটাই বিশ্বাস করতে ভালো লাগে। কিন্তু বাস্তবতা মাঝে মাঝে সেই বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে! আমরা যখন দেখি কোনো মানুষ বিপদে পড়েছে-রাস্তার মাঝে আহত, কেউ পড়ে গেছে, কেউ ডাকছে সাহায্যের জন্য- তখন বেশিরভাগ সময় আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আর ভাবতে থাকি, অন্য কেউ নিশ্চয় কিছু করবে। এই নীরবতা, এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া মনোভাবই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট' (Bystander Effect) নামে পরিচিত।
বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট এমন এক মানসিক ও সামাজিক ঘটনা যেখানে একজন ব্যক্তি বিপদে পড়লেও, আশেপাশে বেশি মানুষ থাকলে কেউই সাহায্যে এগিয়ে আসে না। বরং যত বেশি দর্শক বা উপস্থিত লোক থাকে, প্রতিজন তত কমভাবে নিজেকে দায়িত্ববান মনে করে। অর্থাৎ, ভিড় যত বড় হয়, ব্যক্তিগত দায়িত্ব তত ছোট হয়ে যায়।এই ঘটনাটি প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৬৪ সালে নিউ ইয়র্কে কিটি জেনোভেস (Kitty Genovese) নামের এক তরুণীর হত্যাকাণ্ডের পর। আশেপাশের ডজনখানেক মানুষ ঘটনার শব্দ শুনেও কেউ পুলিশে খবর দেয়নি বা সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কারণ, সবাই ভেবেছিল, অন্য কেউ নিশ্চয়ই করবে।এই ঘটনার পর মনোবিজ্ঞানীরা গভীরভাবে মানুষের এই আচরণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।
কেন ঘটে এই মানসিক স্থবিরতা?
বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, বরং এটি মানুষের মস্তিষ্কের সামাজিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার একটি ফলাফল। নিচে এর মূল মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো তুলে ধরা হলো-
⇨ Diffusion of Responsibility (দায়িত্ববোধের বিলোপ): যখন আমরা একা থাকি, তখন সাহায্য করার সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট। কিন্তু যখন আশেপাশে অনেক মানুষ থাকে, তখন প্রত্যেকে ভাবে, "অন্য কেউ নিশ্চয় করবে।"ফলে দায়িত্ব সবার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, আর শেষমেশ কেউই করে না।
মস্তিষ্কের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অংশ (prefrontal cortex) তখন অন্যদের উপস্থিতি দেখে নিজেকে গৌণ ভাবতে শুরু করে।
⇨ Social Influence (সামাজিক প্রভাব):
আমরা সামাজিক প্রাণী, তাই আচরণের ক্ষেত্রে অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখে সিদ্ধান্ত নেই। যদি কেউ বিপদে পড়ে এবং বাকিরা নীরব থাকে, আমরা ধরেই নিই, হয়তো ব্যাপারটা তত গুরুতর নয়। এটি ঘটে informational social influence-এর কারণে, যেখানে আমরা অন্যদের আচরণকেই সঠিক ধরে নিই, এমনকি নিজের চোখে বিপদ দেখেও।
⇨ Fear of Misjudgment (ভুল বোঝার ভয়): অনেকে ভাবেন, "যদি ভুল বুঝে ফেলি?" বা "যদি সবাই ভাবে আমি বাড়াবাড়ি করছি?"-এই ভয় মস্তিষ্কে সামাজিক অস্বস্তির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে (amygdala সক্রিয় হয়), ফলে আমরা পদক্ষেপ নিতে দেরি করি।
⇨ Pluralistic Ignorance (সমষ্টিগত অজ্ঞতা): সবাই যখন দেখে কেউ কিছু করছে না, তখন ভুলভাবে ধরে নেয়-"অবশ্যই সাহায্যের দরকার নেই।" এই পারস্পরিক ভুল অনুমানই পুরো ভিড়কে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।
⇨ Evaluation Apprehension (মূল্যায়নের ভয়): মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, অন্যরা তাকে কেমনভাবে দেখছে তা নিয়ে চিন্তা করা। বিপদের মুহূর্তে এগিয়ে গেলে যদি কেউ ঠাট্টা করে বা বিচার করে, এই ভয়ও মানুষকে আটকে দেয়।
গবেষণা যা বলে-
মনোবিজ্ঞানের দুটি গবেষক, জন ডারলে (John Darley) ও বিব লাতানে (Bibb Latané) ১৯৬৮ সালে একাধিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট প্রমাণ করেন। তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের এমন অবস্থায় রাখা হয় যেখানে তারা ভাবতেন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা সাহায্য চাচ্ছে। ফলাফল আশ্চর্যজনক—
একজন অংশগ্রহণকারী একা থাকলে ৮৫% সময়েই সাহায্যে এগিয়ে আসে,কিন্তু যদি আশেপাশে আরও কয়েকজন উপস্থিত থাকে, তখন সেই হার নেমে যায় ৩০% বা তারও কমে।
এই গবেষণাগুলোই প্রথমবার বৈজ্ঞানিকভাবে দেখায়, উপস্থিত মানুষের সংখ্যা বাড়লে সাহায্যের প্রবণতা কমে যায়, যা মূলত দায়িত্ববোধের বিচ্ছুরণের (diffusion) ফলাফল।
বাস্তব জীবনে এর প্রভাব-
আজকের বিশ্বে এই প্রবণতা আরও তীব্র হচ্ছে, বিশেষ করে স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া যুগে।মানুষ এখন বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করার বদলে ভিডিও তোলে, ছবি তোলে, অনলাইনে পোস্ট দেয়। এর ফলে সহানুভূতি পরিণত হয় দর্শকসুলভ কৌতূহলে। একে অনেক গবেষক বলেন "Digital Bystander Effect", যেখানে প্রযুক্তি মানুষকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে মানবিক দায়িত্ব থেকে। রাস্তার দুর্ঘটনা, নিপীড়ন, আগুন লাগা বা প্রকাশ্য নির্যাতনের সময় মানুষ ভিড় জমায়, কিন্তু পদক্ষেপ নেয় না।
যেভাবে এই প্রবণতা বদলানো সম্ভব-
☞ ব্যক্তিগত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রথমে বুঝতে হবে, বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট বাস্তব। যখনই কোনো জরুরি পরিস্থিতি দেখবেন, ভাববেন না অন্য কেউ করবে। এক মুহূর্তের দেরি কারো জীবনের দাম হতে পারে।
☞ স্পষ্ট নির্দেশ দিন! যদি একা সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে নির্দিষ্টভাবে কাউকে নির্দেশ দিন, "আপনি, দয়া করে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করুন।" এতে দায়িত্ব আর অস্পষ্ট থাকে না।
☞ সহানুভূতি ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল, কর্মস্থল বা সমাজে "first aid" ও "emergency response" ট্রেনিং দিলে মানুষ জানবে কীভাবে কাজ করতে হয়।
সহমর্মিতা চর্চা করাও বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট কমাতে সাহায্য করে।
☞ সামাজিক নীরবতা ভাঙতে হবে। বিপদের মুহূর্তে প্রথম যে কথা বলে বা প্রথম যে এগোয়, সে-ই বাকিদের অনুপ্রাণিত করে। একটি পদক্ষেপই পুরো ভিড়ের মনোভাব বদলে দিতে পারে।
বাইস্ট্যান্ডার ইফেক্ট আমাদের শেখায়, মানুষ একসাথে থাকলেই মানবিক হয় না। কখনও কখনও জনসমাগমই সবচেয়ে বড় নীরবতা তৈরি করে। এই প্রবণতা শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, সামাজিক মূল্যবোধের পরীক্ষাও। মানবতার আসল শক্তি তখনই প্রকাশ পায়, যখন কেউ ভয় না পেয়ে প্রথমে হাত বাড়ায়।
একজনের সিদ্ধান্তেই হয়তো বদলে যেতে পারে আরেকজনের জীবন, এমনকি পুরো সমাজের মানসিকতা। তাই পরের বার যখন দেখবেন কেউ বিপদে, এক মুহূর্ত থেমে ভাবুন,যদি সবাই ভাবে অন্য কেউ করবে, তাহলে কেউ-ই করবে না!
আপনার প্রতিক্রিয়া জানান
মন্তব্যসমূহ
এই সংবাদের জন্য এখনো কোনো মন্তব্য নেই।